বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস
প্রকাশ : ২১ মে ২০২৫, ১৭:০৪ | অনলাইন সংস্করণ
কমল চৌধুরী:
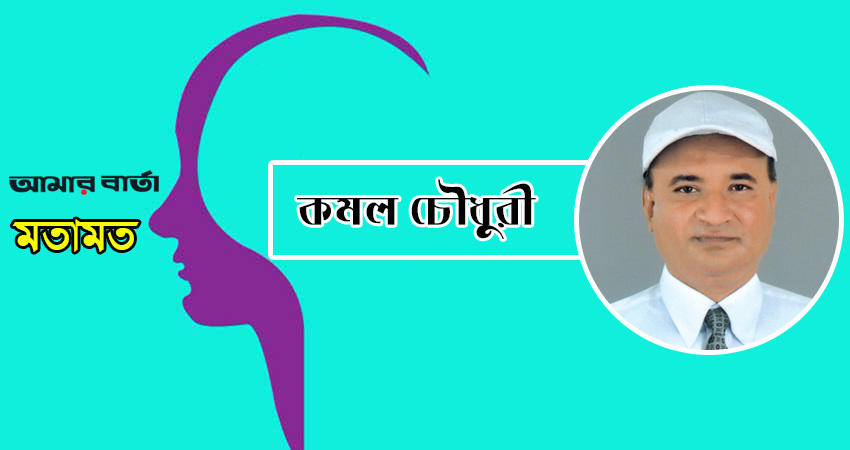
বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি প্রধান উন্নয়নশীল মিশ্র অর্থনীতি। দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি নামমাত্র অর্থে বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম এবং ক্রয়ক্ষমতার সমতার দিক থেকে ২৫তম বৃহত্তম। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশকে পরবর্তী একাদশের মধ্যে একটি হিসেবে দেখে। এটি সীমান্ত বাজার থেকে উদীয়মান বাজারে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে, বিশ্বব্যাপী মহামারীর পর বাংলাদেশ ৭.২% জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নিবন্ধন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি।
ভারত বিভক্তির পর শ্রম সংস্কার এবং নতুন শিল্পের কারণে বাংলাদেশে শিল্পায়ন একটি শক্তিশালী গতি পায়। [১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের রপ্তানির ৭০% থেকে ৫০% এর মধ্যে উৎপাদিত হয়েছিল। আধুনিক বাংলাদেশ ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে, যার ফলে মুক্তবাজার এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের প্রসার ঘটে। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে, দেশে একটি ক্রমবর্ধমান তৈরি পোশাক শিল্প ছিল। ১৬ মার্চ ২০২৪ সালের হিসাবে, বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ সবুজ পোশাক কারখানা রয়েছে, যাদের শক্তি ও পরিবেশগত নকশায় নেতৃত্ব (খঊঊউ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (টঝএইঈ) থেকে সার্টিফিকেশন রয়েছে, যেখানে ৮০টি প্লাটিনাম-রেটেড, ১১৯টি স্বর্ণ-রেটেড, ১০টি রূপা-রেটেড, এবং চারটি কোনও রেটিং ছাড়াই। ৬ মার্চ ২০২৪ সালের হিসাবে, বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০০টি খঊঊউ সবুজ পোশাক কারখানার মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশে অবস্থিত, যার মধ্যে শীর্ষ ১০টির মধ্যে ৯টি এবং শীর্ষ ২০টির মধ্যে ১৮টি রয়েছে। ২৭ এপ্রিল ২০২৪ সালের হিসাবে, বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান ঔষধ শিল্প রয়েছে যার গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১২ শতাংশ। ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারণ স্থানীয় কোম্পানিগুলি ওষুধের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে। বৃহৎ পরিসরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের কৃষি সরকারী ভর্তুকি দ্বারা সমর্থিত এবং খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন অনুসরণ করেছে। মহামারীর পর বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামোগত উন্নতি, ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য প্রবাহ। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে প্রচুর পরিমাণে অ-কার্যকর ঋণ বা ঋণ খেলাপি রয়েছে, যা অনেক উদ্বেগের কারণ হয়েছে। বেসরকারি খাত জিডিপির ৮০%। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ দেশের দুটি স্টক মার্কেট। বেশিরভাগ বাংলাদেশি ব্যবসা বেসরকারি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) যা সমস্ত ব্যবসার ৯০%।
অর্থনৈতিক ইতিহাস:
পাঞ্চ-চিহ্নিত মুদ্রা হল বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মুদ্রার প্রাচীনতম রূপ, যা লৌহ যুগ এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সময় থেকে শুরু। বাংলাদেশে হারকিউলিসের ছবি সম্বলিত প্রথম শতাব্দীর রোমান মুদ্রা খনন করা হয়েছে এবং রোমান বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক সংযোগের ইঙ্গিত দেয়। রোমান ভূগোলবিদ ক্লডিয়াস টলেমি কর্তৃক উল্লিখিত উয়ারী-বটেশ্বর ধ্বংসাবশেষকে সৌনাগৌরার (বাণিজ্য কেন্দ্র) এম্পোরিয়াম বলে মনে করা হয়। বাংলার পূর্ব অংশটি ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। গঙ্গা বদ্বীপটি মৃদু, প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু, উর্বর মাটি, প্রচুর জল এবং প্রচুর মাছ, বন্যপ্রাণী এবং ফলের সুবিধা প্রদান করেছিল। অভিজাতদের জীবনযাত্রার মান ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, টি হর্স রোড এবং সিল্ক রোডের মতো বাণিজ্য পথগুলি এই অঞ্চলটিকে বৃহত্তর পাড়ার সাথে সংযুক্ত করেছিল। ৪০০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে, এই অঞ্চলে ভূমি মালিকানা, কৃষি, পশুপালন, জাহাজ চলাচল, ব্যবসা, বাণিজ্য, কর এবং ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে একটি উন্নত অর্থনীতি ছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং আরবদের পারস্য-বাণিজ্য রুট দখলের পর বাংলার সাথে মুসলিম বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এই বাণিজ্যের বেশিরভাগই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় মেঘনা নদীর পূর্ব দিকে ঘটেছিল। ১২০৪ সালের পর, মুসলিম বিজেতারা প্রাক-ইসলামিক রাজ্যগুলির সোনা ও রূপার মজুদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।বাংলা সালতানাত নিজস্ব একটি বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছিল। বাংলা জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের অন্যান্য অংশে বৃহত্তম জাহাজ ছিল বাণিজ্য নেটওয়ার্ক। জাহাজ মালিক বণিকরা প্রায়শই সুলতানের রাজকীয় দূত হিসেবে কাজ করত। মালাক্কায় বিপুল সংখ্যক ধনী বাঙালি বণিক এবং জাহাজ মালিক বাস করতেন। বাংলার একটি জাহাজ ব্রুনাই এবং সুমাত্রা থেকে চীনে দূতাবাস পরিবহন করত। বাংলা এবং মালদ্বীপ ইতিহাসের বৃহত্তম শেল মুদ্রা নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত। আফ্রিকার মালিন্দি থেকে একটি মাসাই জিরাফ বাংলায় পাঠানো হয়েছিল এবং পরে বাংলার সুলতানের উপহার হিসেবে চীনের সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। আরাকানের শাসকরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানীর জন্য বাংলার দিকে তাকিয়েছিলেন। মুঘল শাসনামলে, বাংলা বিশ্বব্যাপী মসলিন, রেশম এবং মুক্তা ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। অভ্যন্তরীণভাবে, ভারতের বেশিরভাগ অংশ চাল, রেশম এবং তুলা বস্ত্রের মতো বাঙালি পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিদেশে, ইউরোপীয়রা তুলা বস্ত্র, সিল্ক এবং আফিমের মতো বাঙালি পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল; এশিয়া থেকে ডাচ আমদানির ৪০% বাংলার ছিল, উদাহরণস্বরূপ। বাংলা ইউরোপে লবণাক্ত পদার্থ পাঠাত, ইন্দোনেশিয়ায় আফিম বিক্রি করত, জাপান ও নেদারল্যান্ডসে কাঁচা রেশম রপ্তানি করত এবং ইউরোপ, ইন্দোনেশিয়া ও জাপানে রপ্তানির জন্য তুলা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন করত। ১৮ শতকের বাংলার প্রকৃত মজুরি এবং জীবনযাত্রার মান ব্রিটেনের সাথে তুলনীয় ছিল, যেখানে ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ জীবনযাত্রার মান ছিল। মুঘল আমলে, তুলা উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল বাংলা, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার আশেপাশে, যার ফলে মধ্য এশিয়ার মতো দূরবর্তী বাজারে মসলিনের ডাক আসত।বাঙালি কৃষিবিদরা দ্রুত তুঁত চাষ এবং রেশম চাষের কৌশল শিখে নেন, যার ফলে বাংলা বিশ্বের একটি প্রধান রেশম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এশিয়া থেকে ডাচরা আমদানি করা ৫০% বস্ত্র এবং প্রায় ৮০% রেশম বাংলায় ছিল। বাংলায় একটি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ শিল্পও ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার জাহাজ নির্মাণ উৎপাদন ছিল বার্ষিক ২২৩,২৫০ টন, যেখানে ১৭৬৯ থেকে ১৭৭১ সাল পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার উনিশটি উপনিবেশে ২৩,০৬১ টন উৎপাদন হত। এই অঞ্চলটি জাহাজ মেরামতেরও একটি কেন্দ্র ছিল। তৎকালীন ইউরোপীয় জাহাজ নির্মাণের তুলনায় বাংলার জাহাজ নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ছিল বাংলায় ফ্লাশড ডেক ডিজাইনের প্রবর্তন। জাহাজ নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ছিল - চালের জাহাজ, যার ফলে হালগুলি শক্তিশালী ছিল এবং স্টেপড ডেক ডিজাইন দিয়ে নির্মিত ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় জাহাজের কাঠামোগতভাবে দুর্বল হালের তুলনায় কম ফুটো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরবর্তীতে ১৭৬০-এর দশকে বাংলার চালের জাহাজের ফ্লাশ-ডেক এবং হাল-নকশাগুলির নকল করে, যার ফলে শিল্প বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় জাহাজগুলির সমুদ্রের যোগ্যতা এবং নৌচলাচলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।উপনিবেশিক-পূর্ব এবং মুঘল আমলের প্রাচীনতম ব্যবসাগুলির মধ্যে, ফখরুদ্দিনের বিরিয়ানি রেস্তোরাঁটি বাংলার নবাবদের যুগে তার ইতিহাসের চিহ্ন খুঁজে পায়।
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যারা ১৭৯৩ সালে নিজামত (স্থানীয় শাসন) বিলুপ্ত করে বাংলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, দক্ষিণ এশিয়ায় কোম্পানি-অধিষ্ঠিত অঞ্চলগুলির জন্য তাদের বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা, বর্তমানে পশ্চিম বাংলার রাজধানী শহরকে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর পূর্ব বাংলার উন্নয়ন কেবলমাত্র কৃষিতে সীমাবদ্ধ ছিল। আঠারো এবং উনিশ শতকের শেষের দিকের প্রশাসনিক অবকাঠামো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রক্রিয়াকরণকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষি-উৎপাদক - প্রধানত চাল, চা, সেগুন, তুলা, আখ এবং পাটের - হিসাবে পূর্ব বাংলার কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ব্রিটিশ শাসন রেলপথের প্রবর্তন দেখেছিল। পদ্মা নদীর উপর দিয়ে ট্রেন পরিবহনের জন্য হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, পূর্ব বাংলা এবং আসাম ব্রিটিশ রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব বাংলায় কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং বিনিয়োগের প্রচারের জন্য। ১৯২৮ সালে, চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্রিটিশ ভারতের একটি “প্রধান বন্দর” হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলা তার ধানের অর্থনীতি ব্রিটিশ বার্মার আরাকান বিভাগে প্রসারিত করে। গোয়ালন্দ ঘাট, ঢাকা বন্দর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দর সহ পূর্ব বাংলার নদী ও সমুদ্র বন্দরগুলি বাংলা, আসাম এবং বার্মার মধ্যে বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের কিছু শ্রদ্ধেয় এবং প্রাচীন কোম্পানি ব্রিটিশ বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানি, এম. এম. ইস্পাহানি লিমিটেড, জেমস ফিনলে বাংলাদেশ এবং আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। ভারত বিভক্তির ফলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভূগোল বদলে যায়। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকার স্থানীয় কাঁচামাল যেমন পাট, তুলা এবং চামড়ার উপর ভিত্তি করে শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়। কোরিয়ান যুদ্ধের ফলে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের বৃহত্তম পাট প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আদমজী জুট মিলস নারায়ণগঞ্জ বন্দরে নির্মিত হয়। এই কারখানাটি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নের প্রতীক ছিল। জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে উন্নত হতে শুরু করে। ১৯৫৮ সালে শ্রম সংস্কারের ফলে ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ শিল্প বিকাশে উপকৃত হয়। মুক্ত বাজার নীতিগুলি সাধারণত গৃহীত হয়। সরকার একটি শিল্প নীতি প্রচার করে যার লক্ষ্য ছিল আমদানির উপর নির্ভরতা এড়াতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করা। কিছু ক্ষেত্র, যেমন জনসাধারণের ব্যবহার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে চলে আসে। ১৯৫৫ সালে বার্মা তেল কোম্পানি সিলেটে প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের রপ্তানির অংশ ৭০% থেকে ৫০% এ নেমে আসে এবং শাসকরা তথাকথিত দদউন্নয়নের দশক’’ চালু করে। “এর ফলে অসংখ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যা কেবল ১৯৬০-এর দশকেই নয়, বরং তার পরেও নিজেদেরকে প্রভাবিত করে, যেখানে আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়”। বিশ্বব্যাংকের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যান্য তহবিল পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি অর্থায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্ত ব্যবহার করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দকৃত তহবিল প্রকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বীকৃতি। রেহমান সোবহান দ্বি-জাতি তত্ত্বকে দুই অর্থনীতি তত্ত্বে রূপান্তরিত করে যুক্তি দেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে একই দেশের মধ্যে দুটি ভিন্ন অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।
পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পর, বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণ করে, যা আওয়ামী লীগ সরকারের একটি ভুল প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্র সমস্ত ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং ৫৮০টি শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করে। বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং বিধিনিষেধের অধীনে কাজ করতে হত। উদাহরণস্বরূপ, কোম্পানিগুলির উপর মুনাফার সীমা আরোপ করা হত। যে কোনও কোম্পানির রাজস্ব বা মুনাফা সীমার বেশি ছিল, তারা জাতীয়করণের ঝুঁকিতে ছিল। যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানিরা জাতীয়করণকৃত অনেক শিল্প পরিত্যাগ করেছিল; যদিও আওয়ামী লীগপন্থী এবং অন্যান্য বাঙালি ব্যবসারও সম্পত্তি এবং শিল্প জাতীয়করণের ক্ষতি হয়েছিল। জমির মালিকানা ২৫ বিঘার কমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২৫ বিঘার বেশি জমির মালিকদের উপর কর আরোপ করা হত।বাজারের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের তাদের পণ্য বিক্রি করতে হত। খুব কমই কোনও বিদেশী বিনিয়োগ ছিল। যেহেতু বাংলাদেশ একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণ করেছিল, তাই অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদ উৎপাদনের ধীরগতির মধ্য দিয়ে এটি এগিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধকালীন বিঘ্নের কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রধান পণ্যের তীব্র ঘাটতি ছিল। সরবরাহের অস্থিরতা এবং সিন্থেটিক বিকল্পের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে পাটের বহিরাগত বাজার হারিয়ে গিয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ ছিল সীমিত, এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা অবিশ্বাস্য ছিল।যদিও বাংলাদেশের বিশাল কর্মশক্তি ছিল, স্বল্প প্রশিক্ষিত এবং স্বল্প বেতনের শ্রমিকদের বিশাল মজুদ ছিল মূলত নিরক্ষর, অদক্ষ এবং স্বল্প বেকার। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত বাণিজ্যিকভাবে শোষণযোগ্য শিল্প সম্পদের অভাব ছিল। মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে, ৩০০ থেকে ৪০০ শতাংশের মধ্যে ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিবহন ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়েছিল। শত শত সড়ক ও রেলপথ সেতু ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এবং রোলিং স্টক অপর্যাপ্ত এবং খারাপ মেরামতের অধীনে ছিল। নতুন দেশটি এখনও ১৯৭০ সালে এই অঞ্চলে আঘাত হানা একটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় থেকে পুনরুদ্ধার করছিল এবং ২৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটায়। পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম মাসগুলিতে ভারত সমালোচনামূলকভাবে পরিমাপিত অর্থনৈতিক সহায়তা নিয়ে অবিলম্বে এগিয়ে এসেছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারির মধ্যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সহায়তা থেকে বাংলাদেশকে ২৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। আওয়ামী লীগ ঘোড়াশাল সার কারখানা এবং আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কাজ শুরু করে। বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো এবং অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ।
সামরিক শাসন এবং অর্থনৈতিক সংস্কার (১৯৭৫-১৯৯০):
১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের পর, নতুন বাংলাদেশী সামরিক নেতারা বেসরকারি শিল্পকে উৎসাহিত করতে শুরু করেন এবং নতুন শিল্প সক্ষমতা বিকাশ এবং অর্থনীতি পুনর্বাসনের দিকে মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক নেতাদের দ্বারা গৃহীত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মডেলের ফলে অদক্ষতা এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দেয়। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে, সরকার ধীরে ধীওে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে আরও বেশি সুযোগ দেয়, যা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরায় চালু করা হয়। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এবং রপ্তানি শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ঊচত) নামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পগুলিকে তাদের মূল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে অথবা বেসরকারি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে জাতীয়করণ এবং বেসরকারীকরণও করে। সরকারি খাতে অদক্ষতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়; এবং প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে বামপন্থী বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০-এর দশকে প্রাণের মতো গতিশীল স্থানীয় ব্র্যান্ডের উত্থান ঘটে। মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে, গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক এবং প্রশিকার মতো নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে বাংলাদেশ আধুনিক ক্ষুদ্রঋণ শিল্পের পথিকৃৎ হয়ে ওঠে। শিল্প খাতে, ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দুটি নীতিগত উদ্ভাবন রপ্তানিকারকদের সাহায্য করে। এই সংস্কারগুলি বন্ডেড গুদামের মাধ্যমে পরপর ঋণপত্র এবং শুল্ক-প্রলোভন সুবিধা চালু করে। এই সংস্কারগুলি দেশের নবজাতক পোশাক শিল্পের জন্য প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে। এই সংস্কারগুলি একটি পোশাক প্রস্তুতকারককে বিদেশী পোশাক ক্রেতাদের কাছ থেকে ঋণপত্র দেখিয়ে আমদানির জন্য দেশীয় ব্যাংকগুলি থেকে ঋণপত্র পেতে অনুমতি দেয়। এই সংস্কারগুলি আমদানিকৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত শুল্কও পরিশোধ করে, যদি প্রমাণ করা হয় যে বন্ডেড গুদামে সংরক্ষিত উপকরণ রপ্তানি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংস্কারগুলি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেক্সটাইল রপ্তানিকারক খাতে শিল্পের প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, অগ্রগতির উৎসাহজনক লক্ষণ দেখা যায়। বেসরকারি উদ্যোগ এবংবিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিগুলি ত্বরান্বিত করা হয়, সরকারি শিল্পগুলিকে বেসরকারিকরণ করা হয়, বাজেট শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করা হয় এবং আমদানি ব্যবস্থার উদারীকরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ বিনিয়োগ ও বাণিজ্য ব্যাংক বাংলাদেশ, নেপাল এবং মালদ্বীপের জন্য একটি বহুজাতিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
লেখক : নির্বাহী সম্পাদক-দৈনিক সকালের সময় ও দ্যা ডেইলি বেষ্ট নিউজ, ঢাকা।
আমার বার্তা/কমল চৌধুরী/এমই
